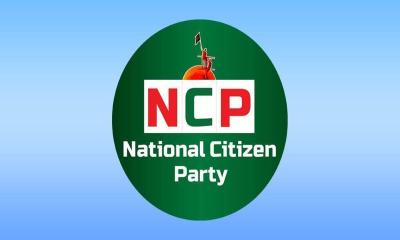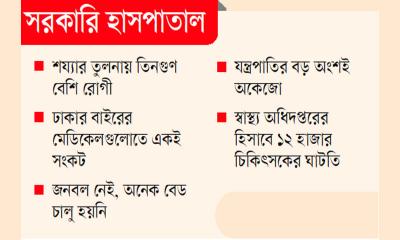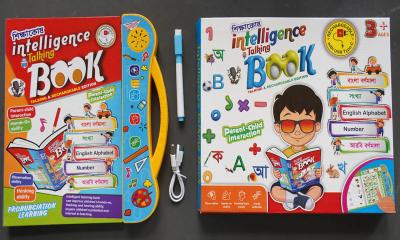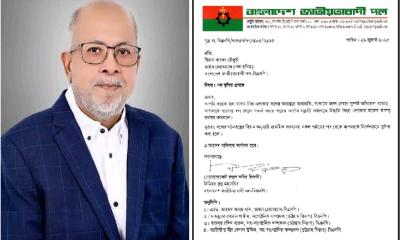রায়হান আহমেদ তপাদার
জুলাই ১৪, ২০২২, ০১:০৭ এএম

বিশ্ব অর্থনীতি ও বাজারসংক্রান্ত সামপ্রতিক আলোচনা একগুচ্ছ প্রশ্ন ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে। বৈশ্বিক দৃশ্যপটে অনেক কিছুই দ্রুত বদলে যাচ্ছে। বিশ্বায়নের এই তুমুল প্রতিযোগিতার যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞান আর গবেষণায় পৃথিবী বদলে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। পুরো বিশ্ব রাজনীতির কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহূত হচ্ছে অস্ত্র এবং বাণিজ্যের প্রতিযোগিতা। যুক্তরাষ্ট্র-চীনের বণিজ্যযুদ্ধ, ইরান সংকট, মধ্যপ্রাচ্যের নানা অস্থিরতা, পুঁজিবাদী শক্তির আগ্রাসন, প্যারিসের জলবায়ু চুক্তিসহ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অবাধ বিস্তার পুরো বিশ্ব অর্থনীতির মোড় পরিবর্তন করছে, যার প্রভাব এশিয়াসহ পুরো পৃথিবীতে উল্লেখযোগ্যভাবে পড়ছে।
বিশ্ব অর্থনীতিতে চীনের উত্থান বিশ্ব বাণিজ্যের মেরুকরণে অনেক চ্যালেঞ্জিং করে তুলেছে। বাংলাদেশ এর ব্যতিক্রম নয়। তবুও স্বল্প ভূমি আর মাত্রাতিরিক্ত জনগণের এই দেশ হাজারো সমস্যাকে মোকাবিলা করে এগিয়ে যাচ্ছে উন্নত বিশ্বে পৌঁছানোর স্বপ্ন নিয়ে। তলাবিহীন ঝুড়ির তকমা ঝেড়ে ফেলে অনেক দূর এগিয়েছে দেশটি, মাথাপিছু আয় বেড়েছে। আয় বাড়ার সাথে সাথে বেড়েছে মানুষের গড় আয়ু। নারীর ক্ষমতায়নে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে এগিয়ে আছে বাংলাদেশ।
মানবসম্পদ ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের সূচেকে ক্রমান্বয়ে উন্নত হচ্ছে। বড় বড় প্রকল্প বাস্তবায়নে বাংলাদেশের সক্ষমতা ক্রমাগত বাড়ছে। পদ্মা সেতুর মতো মেগা প্রজেক্ট নিজস্ব অর্থায়নে করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ, মেট্রোরেল, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, দরিদ্র হূাসকরণ, তথ্য-প্রযুক্তি খাতে বাংলাদেশের অগ্রগতি ঈর্ষণীয়। ২০১৮ সালে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের সব শর্ত পূরণ করেছে। দরিদ্র দেশ হিসেবে বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের যে পরিচয় এক সময় ছিল সেই পরিস্থিতির যথেষ্ট উন্নত হয়েছে গত কয়েক দশকে।
যে স্বাধীন বাংলাদেশের মাত্র কয়েক কোটি টাকার বাজেট নিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল, সেই দেশের বাজেট আজ ছয় লাখ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। ছোট্ট অর্থনীতির দেশটি আজ পরিচিতি পেয়েছে এশিয়ার টাইগার ইকোনমি হিসেবে। কিন্তু বৈশ্বিক বাস্তবতার নিরিখে প্রথম প্রশ্নটি বেশ সহজ। আর সেটি হলো, মন্দা কি বিস্তৃত ও গভীর হচ্ছে? সামপ্রতিক সময়ে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) মতো প্রতিষ্ঠান বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন তাৎপর্যজনকভাবে কমিয়েছে।
আরও কমানোর আশঙ্কা আছে। বর্তমানে এটি উদ্বেগের একটা কারণ। একটি বিশ্বমন্দা-পরপর দুই প্রান্তিকে ঋণাত্মক জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয়তো হবে না, কিন্তু সংঘাতের নাটকীয় বিস্তার কিংবা জ্বালানির মতো গুরুত্বপূর্ণ বাজার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার মতো বড় কোনো অভিঘাত এ চিত্র বদলে দিতে পারে। অবশ্য কিছু অর্থনীতি নিশ্চিতভাবে সংকুচিত হবে। তেল ও গ্যাসের উচ্চমূল্য সত্ত্বেও ভয়াবহ ও প্রলম্বিত পশ্চিমা অবরোধের কারণে রাশিয়ার জিডিপি অবশ্যই কমবে। উচ্চ জ্বালানি মূল্য, জীবাশ্ম জ্বালানি আমদানির ওপর ব্যাপক নির্ভরতা এবং রাশিয়ার সরবরাহ ব্যবস্থা থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেয়ার বাধ্যবাধকতায় ইউরোপও মন্দার মুখোমুখি হতে পারে। মহামারির প্রভাবের সঙ্গে বেড়ে চলা খাদ্য ও জ্বালানি মূল্যের কারণে আবার অনেক নিম্ন আয়ের দেশও কঠিন সময় পার করছে।
এদিকে যুক্তরাষ্ট্র অব্যাহতভাবে বড় কোনো অর্থনৈতিক অধোগতির মুখোমুখি হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে, যদিও সেখানে মন্দা অবশ্য প্রত্যাশিত দৃশ্যপট নয়। একইভাবে বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম শক্তিশালী ইঞ্জিন চীন অন্তত এক বছর ধরে এক অঙ্কের নিম্ন প্রবৃদ্ধির অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এটা মূলত কোভিড লকডাউনের সম্মিলিত প্রভাব, বয়োজ্যেষ্ঠদের মধ্যে টিকা নেয়ার নিম্নহার, উচ্চ প্রবৃদ্ধির প্রযুক্তি খাতে বিনিয়োগজনিত আস্থাহীনতা এবং উচ্চঋণ ও পড়তি দামে জর্জরিত আবাসন খাতের কারণে। অপর গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি মূল্যস্ফীতি সংক্রান্ত।
সামপ্রতিক মূল্যবৃদ্ধির নিকট কারণ সরবরাহ ব্যবস্থার প্রতিবন্ধকতা এবং জোগান ও চাহিদার ভারসাম্যহীনতা। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ জ্বালানি, ভোগ্যপণ্য ও খাদ্যের দামের ওপর ঊর্ধ্বমুখী চাপ তীব্রতর করেছে। এর কিছুটা সাময়িক, যদিও তা প্রাথমিক প্রত্যাশার চেয়ে দীর্ঘ সময় ধরে বজায় থাকবে। তবে মূল্যস্ফীতি ক্রমেই তেতে উঠছে। শিগগিরই প্রশমন হবে বলে মনে হচ্ছে না। বিশ্ব অর্থনীতির প্রতিনিধিত্বকারী প্রায় ৭৫ শতাংশ জনসংখ্যা বয়োবৃদ্ধ হচ্ছে, শ্রমশক্তির অংশগ্রহণ কমছে এবং উৎপাদনশীলতা প্রবৃদ্ধি নিম্নমুখী হচ্ছে।
আবার উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে অব্যবহূত সক্ষমতার ব্যবধান আগের চেয়ে কমে আসছে বটে, তবু তার মধ্যে একটা অংশ অব্যবহূত থাকছে। এ ছাড়া সরবরাহ ও চাহিদা সংযোগের সামনের নীতিচালিত বৈচিত্র্যের প্রভাব এবং মধ্যস্থিত মূল্যস্ফীতি মূলক চাপসহ সরবরাহ-প্রতিবন্ধক প্রবৃদ্ধির প্রলম্বিত সময় পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে। অন্য প্রশ্নটি হলো প্রযুক্তি খাত ও ডিজিটাল রূপান্তরের পরবর্তী ধাপ কী হবে? লকডাউন এবং অন্য জনস্বাস্থ্য পদক্ষেপগুলো মহামারির সময়ে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার বেগবান করেছে। তবে বাজার প্রত্যাশার বিপরীতে এ প্রবণতা মনে হয় ধীর হচ্ছে, যেহেতু মহামারির বিধিনিষেধ উঠিয়ে দেয়া হয়েছে।
আশাবাদী প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলনের মধ্যেও শেয়ারবাজারে এমন ভ্যালুয়েশন হয়েছে যা অনেকটা অবাস্তব। মূল্যস্ফীতির প্লাবন, আর্থিক কৃচ্ছ্রতা এবং নিম্নমুখী প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলনের এ সময়ে বাজার সংশোধন হওয়া শুরু হয়েছে। বিস্ময়ের নয়, গ্রোথ স্টক-প্রত্যাশিত ভবিষ্যৎ নগদ প্রবাহ থেকে যার মূল্য আসে এবং যেটা প্রযুক্তি খাতে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে লক্ষণীয়ভাবে কমেছে। এসব বাজার ওঠানামার মানে এই নয় যে চলমান ডিজিটাল, জ্বালানি ও বায়োমেডিকেল রূপান্তরের তেমন গুরুত্ব নেই কিংবা সেগুলোর দীর্ঘস্থায়ী অর্থনৈতিক প্রভাব থাকবে না। অদূর ভবিষ্যতে প্রতিবিম্বিত অন্তর্নিহিত অর্থনৈতিক বাস্তবতার চেয়ে স্বাভাবিকভাবে বাজার আরও বেশি উদ্বায়ী হবে। এমনকি উচ্চতর বাজার উদ্বায়িতার গুরুত্বপূর্ণ স্বল্পমেয়াদি প্রভাব থাকবে।
কারণ উদ্ভাবনমূলক, সম্ভাবনাময় উচ্চ প্রবৃদ্ধির কোম্পানিকে সমর্থন প্রদানে ভূমিকা রাখা ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ও প্রাইভেট ইক্যুইটি বাজারের উত্তাপ থেকে সুরক্ষিত নয়। ঊর্ধ্বমুখিতার সময় ভ্যালুয়েশন বাড়ে এবং টেকসই প্রবৃদ্ধি ডিনামিক্সের প্রবঞ্চনাপূর্ণ দাবি করা কিছু কোম্পানি অর্থায়িতও হয়। সামপ্রতিক সময়ে যে চূড়ান্ত প্রশ্নটি মানুষের মনে আচ্ছন্ন হয়ে আছে তা হলো, রাশিয়ার তেল ও গ্যাসের ওপর নির্ভরতা কমানোর ইউরোপীয় সমাধান এবং জীবাশ্ম জ্বালানির আকাশছোঁয়া দাম নিম্ন কার্বন ট্রানজিশন বিচ্যুৎ করবে কি না। সৌভাগ্যজনকভাবে চিন্তা করার ভালো কারণ আছে সেটি হবে না, অন্তত দীর্ঘস্থায়ী উপায় হিসেবে।
এদিকে জীবাশ্ম জ্বালানির উচ্চমূল্য বিভিন্ন দেশ ও ভোক্তাদের জন্য জ্বালানি দক্ষতা বাড়ানো এবং টেকসই জ্বালানি সলিউশনে বিনিয়োগ করতে জোরালো প্রণোদনা দেয়। এদিক থেকে তারা একটি কার্যকর বৈশ্বিক কার্বন প্রাইসিং স্কিম প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা পরিবর্তনে কিছুটা এগিয়েছে নিবর্তনমূলক করের প্রভাবে জীবাশ্ম জ্বালানির উচ্চমূল্য দেশের ভেতরে ও আন্তঃদেশগুলোর মধ্যে বণ্টনমূলক প্রতিকূল প্রভাব পড়বে। তবে আয় পুনর্বণ্টনের কিছু প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এ ধরনের প্রভাব প্রশমন করা যেতে পারে।
সরকারের যেটা করা উচিত নয় তা হলো, চূড়ান্ত দাম বাজারের নিচে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জীবাশ্ম জ্বালানি সাশ্রয়ী রাখা, যেহেতু এটি আরও টেকসই সুযোগ উন্মোচনের প্রেষণা দুর্বল করবে। বিকল্প উৎস বা উপায়ে বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে জ্বালানি মূল্য স্থিতিশীল রাখার একটা ভালো যুক্তি আছে। কিন্তু তার মানে এটি নয় যে ত্রুটি রেখেই দাম কমাতে হবে। ভূরাজনীতিও ক্লিন এনার্জির প্রতি আগ্রহ বাড়িয়ে তুলছে। জীবাশ্ম জ্বালানির মতো নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রধানত বহিস্থ নির্ভরতা তৈরি করে না। কাজেই সবুজ রূপান্তরের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত এবং জ্বালানি সরবরাহকে হাতিয়ার বানানো সৃষ্ট অরক্ষণীয়তা হ্রাসের শক্তিশালী ম্যাকানিজম খুঁজতে হবে।
গ্রিন ট্রানজিশন একটি বহু দশকের প্রক্রিয়া, যে সময়ে বিশ্ব জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে ধীরে ধীরে পরিচ্ছন্ন জ্বালানির দিকে যাত্রা করবে। স্বল্পমেয়াদে বিশেষ করে ইউরোপের অর্থনীতিগুলো চাহিদা মেটাতে কয়লাসহ ডার্টি এনার্জির ব্যবহার বাড়াতে পারে। কিন্তু সেটি বৈশ্বিক স্থায়িত্বশীলতা ও এনার্জি ট্রানজিশনের জন্য বিপর্যয়কর হবে না বলে অনুমান।
অন্যদিকে আবারও কোল্ডওয়ার বা শীতলযুদ্ধের মতো একটি পরিস্থিতিতে বিশ্ব ধীরে ধীরে প্রবেশ করছে। চীনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। সামনে এটা বাড়তে পারে। ভারত-চীন সীমান্ত উত্তেজনা রয়েছে। ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ক আরও নিচের দিকে গেছে। ইউক্রেন নিয়ে রাশিয়ার সঙ্গে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো খুব দ্বন্দ্বের মধ্যে রয়েছে। ইসরায়েল-ইরান উত্তেজনা আরেকটি সমস্যা। সমপ্রতি চীনকে মোকাবিলায় যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও অস্ট্রেলিয়া মিলে নতুন প্রশান্ত মহাসাগরীয় সামরিক জোট—অকাস গড়ে তুলেছে।
একই উদ্দেশ্যে জাপানের সামরিক তৎপরতা বাড়ছে এবং ভারত, জাপান, অস্ট্রেলিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র মিলে আরেকটি জোট—কোয়াড গঠন করেছে। এর বিপরীতে বড় আকারে চীন-রাশিয়ার যৌথ সামরিক মহড়া দেখা গেছে। এ ছাড়া তাইওয়ান নিয়ে চীন-যুক্তরাষ্ট্র উত্তেজনা চলছে। গত ৫০ বছরে বিশেষ করে ভিয়েতনাম যুদ্ধের পর আমরা কখনো এত বেশি এলাকায় এত বেশি যুদ্ধ-যুদ্ধ ভাব দেখিনি। স্নায়ুযুদ্ধোত্তর সময়ে গত ৩০ বছরে যুক্তরাষ্ট্র ছোট ছোট কয়েকটি দেশে আক্রমণ করলেও সেটাকে বৈশ্বিকভাবে ততটা নাড়া দেয়নি।
কিন্তু এখন যুদ্ধের চেয়েও এই যুদ্ধ-যুদ্ধ ভাব এবং বিশ্বনেতাদের রক্ষণশীল মনোভাব স্নায়ুযুদ্ধের বার্তা দিচ্ছে, যা বিশ্ব অর্থনীতিকে নাড়া দিতে পারে চরমভাবে। অতীতের যেকোনো সময়ের তুলনায় বৈশ্বিক অর্থনীতি এখন অনেক বেশি আন্তঃসংযুক্ত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বেশির ভাগ অর্থনীতিই নির্ভর করত অভ্যন্তরীণ চাহিদার ওপর।
তবে আমাদের আশার কথা হচ্ছে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অক্সিজেনের মতো গুরুত্ব বহন করা খাতটি হলো রেমিট্যান্স। আমদের বেশির ভাগ রেমিট্যান্স যেহেতু মধ্যপ্রচ্যের দেশ থেকে আসে সেক্ষেত্রে নয়া একটি চ্যালেঞ্জের আবির্ভাব হয়েছে। কারণ বিশ্ববাজারে মধ্যপ্রাচ্যের তেল রাজনীতি, অভ্যন্তরীণ সংঘাত ও পশ্চিমাদের ষড়যন্ত্রের জালে আড়ষ্ট হয়ে তাদের অর্থনীতি বহুমুখি ঝুঁকিতে রয়েছে।
এছাড়া মধ্য এশিয়ার দেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন সম্ভামনাময় রাষ্ট্রে শ্রমিকের যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। তাই আমাদের ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে দক্ষ করে গড়ে তুলে এই সুযোগটির যথাপোযুক্ত কাজে লাগাতে পারলে অর্থনীতি আরও বেগবান হবে। কিন্তু সমস্যা হলো আজকের রাজনীতিবিদরা অর্থনৈতিক সমস্যার অর্থনৈতিক সমাধান না করে রাজনৈতিক সমাধান দিতে চান আর রাজনৈতিক সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান না করে অর্থনৈতিক সমাধান দিতে চান। অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি হলো বেসরকারি খাত। কিন্তু এ খাতে বিনিয়োগ দীর্ঘদিন ধরে ২০ থেকে ২২ শতাংশের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। ফলে যে হারে প্রবৃদ্ধি বাড়ছে, সেই হারে কর্মসংস্থান বাড়ছে না। বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ না বাড়লে কর্মসংস্থানও বাড়বে না।
বাংলাদেশে অর্থনীতি দ্রুত বিকাশ লাভ করলেও সহজ ব্যবসার সূচকে অনেক পিছিয়ে আছে। বিশ্বব্যাংকের ব্যবসা-বাণিজ্য সহজ করার সূচকে এবার ১৯০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৬৮তম। দুর্নীতি ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতাসহ বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা আর্থিক খাতের সুশাসন ব্যাহত করছে। সবকিছু মিলিয়ে উদ্যোক্তারা দেশে নতুন বিনিয়োগ করতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। এক্ষেত্রে আর্থিক খাতে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার ও সার্বিক ব্যবসার পরিবেশ উন্নত করার কোনো বিকল্প নেই। তবে আশার কথা হলো, ব্যবসা সহজীকরণের কারণে দক্ষিণ এশিয়ায় বিদেশি বিনিয়োগের অন্যতম কেন্দ্র হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ।
লেখক : গবেষক ও কলামিস্ট