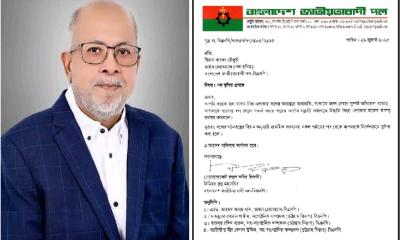ডেভিড বার্গম্যান
আগস্ট ৫, ২০২৫, ০২:১১ পিএম

২০২৪ সালের ১৬ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও আওয়ামী লীগের কর্মীদের গুলিতে শত শত মানুষ নিহত এবং হাজারো মানুষ আহত হন। পাশাপাশি বিক্ষোভকারীদের হাতেও কিছু মৃত্যুর ঘটনা ঘটে।
এসব ঘটনায় দায়ী ব্যক্তিদের বিচারের আওতায় আনার বিষয়টি গত বছরের ৮ আগস্ট দায়িত্ব নেওয়া অন্তর্বর্তী সরকারের জন্য সবচেয়ে কঠিন বিষয়গুলোর একটি হয়ে দাঁড়ায়।
প্রায় এক বছর পর সরকার এই বিচারপ্রক্রিয়ায় কতটা সফল হয়েছে, তা মূল্যায়নের প্রয়োজন রয়েছে। এখানে ‘প্রক্রিয়া’ শব্দটি ব্যবহার করাই যথার্থ।
কারণ, তদন্ত সঠিক এবং বিচারিক কার্যক্রম ন্যায্য হলেই জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা দ্রুত হয় না। তাই এখনো কোনো মামলার নিষ্পত্তি না হওয়াকে একচেটিয়াভাবে ব্যর্থতার নিদর্শন হিসেবে দেখা উচিত নয়।
একজন কৌঁসুলির দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধসংক্রান্ত যে বিচারগুলো এক দশক আগে হয়েছিল, তার তুলনায় বর্তমান পরিস্থিতি প্রমাণসমৃদ্ধ। কারণ, এখানে ভিডিও ফুটেজ ও টেলিফোন যোগাযোগের রেকর্ড পাওয়া সহজ। এ
ছাড়া ২০২৪ সালের জুলাই–আগস্টের ঘটনা অতি সম্প্রতি ঘটায় পর্যাপ্ত ও নির্ভরযোগ্য প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য পাওয়া যাচ্ছে। এসব উপাদান থাকায় কৌঁসুলির জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী মামলা উপস্থাপন করা সহজ হয়ে গেছে। মামলাগুলোকে শক্তিশালী করার জন্য এমন কোনো উপায় অবলম্বনের প্রয়োজন নেই, যা বিচারপ্রক্রিয়াকে প্রশ্নের মুখে ফেলতে পারে, যে দোষে ১০ বছর আগের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচার কার্যক্রম দুষ্ট ছিল।
বাংলাদেশে জুলাইয়ের আন্দোলন-সংক্রান্ত অপরাধগুলোর জবাবদিহি নিয়ে দুটি সমান্তরাল ফৌজদারি ব্যবস্থা চলছে। প্রথমটি হলো, ভুক্তভোগী বা তাঁদের পরিবারের সদস্যদের থানায় করা মামলাগুলো, যা ‘প্রাথমিক তথ্যবিবরণী’ (এফআইআর) আকারে নথিভুক্ত হয়েছে। এসব অভিযোগে বলা হয়েছে, শত শত মানুষ—প্রধানত স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী এবং দলের সুপরিচিত সমর্থকেরা নির্দিষ্ট মৃত্যু বা আহত হওয়ার ঘটনার সঙ্গে জড়িত। তারাই হত্যাকাণ্ড বা হত্যাচেষ্টার অপরাধে দোষী।
দ্বিতীয়টি হলো, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে (আইসিটি) করা মামলাগুলো, যা মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগের আওতায় বিচারাধীন।
সাধারণ আদালত
জুলাইয়ের আন্দোলন নিয়ে ১৭ জুলাই পর্যন্ত করা ১ হাজার ৬০১ মামলার মধ্যে ৬৩৭টি হত্যা মামলা। এসব মামলায় হাজার হাজার না হলেও শত শত মানুষকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে এফআইআরে যাঁদের নাম রয়েছে, তাঁদের মধ্যে অনেকে আছেন, যাঁরা আন্দোলনের সময় প্রকৃতপক্ষে অপরাধ করেছেন এবং সে কারণে তাঁদের গ্রেপ্তার আইনসংগত হতে পারে।
কিন্তু যে মুহূর্তে কারও নাম একটি এফআইআরে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, সেখান থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত—যখন অনেকেই মাসের পর মাস, কেউ কেউ প্রায় এক বছর ধরে গ্রেপ্তার রয়েছেন, চলমান এই বিচারিক ব্যবস্থাটি মূল অপরাধে জড়িত ব্যক্তিদের সঙ্গে নির্দোষ ব্যক্তিদের পার্থক্য নির্ধারণের কোনো বাস্তব প্রয়াস দেখাচ্ছে না।
বাংলাদেশে জুলাইয়ের আন্দোলন-সংক্রান্ত অপরাধগুলোর জবাবদিহি নিয়ে দুটি সমান্তরাল ফৌজদারি ব্যবস্থা চলছে।
অপরাধে জড়িত ও নির্দোষ—দুই শ্রেণির মানুষই গ্রেপ্তারের শিকার হয়েছেন এবং দীর্ঘ সময় ধরে গ্রেপ্তার রয়েছেন। কাউকে গ্রেপ্তার করার ক্ষেত্রে মূল মানদণ্ড প্রমাণ ছিল না; বরং সবচেয়ে বড় বিবেচ্য ছিল তার সঙ্গে আওয়ামী লীগের সম্পর্ক।
এ মুহূর্তে বাংলাদেশে এসব মামলার ক্ষেত্রে যা চলছে, ‘বিচারের আগের আটক’ বা ‘অভিযোগ গঠনের আগের আটক’ নয় (অন্য সবকিছু বাদ দিয়ে শুধু এই দুই ধরনের পদক্ষেপই যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ)। তবু বিষয়টি এখানেই শেষ হয়নি; বরং আরও গুরুতর ও সমালোচনাযোগ্য আরেকটি বিষয় যা ঘটছে, তা হলো ‘তদন্ত শুরুর আগেই আটক’। কিছু ক্ষেত্রে পুলিশ পরে আংশিক তদন্ত করলেও আদালতকে জানায় না যে গ্রেপ্তার ব্যক্তির সঙ্গে অপরাধের কোনো যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়নি।
সরকার বা পুলিশকে এমন হয়রানিমূলক গ্রেপ্তার ঠেকানোর কোনো ধরনের ব্যবস্থা নিতে সময় লেগেছে ৯ মাস। ইতিমধ্যে শত শত, এমনকি হাজার হাজার মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ২০২৫ সালের ৯ এপ্রিল ঢাকার পুলিশ কর্তৃপক্ষের জারি করা এক নির্দেশনায় বলা হয়, জুলাই-আগস্ট মামলায় কাউকে গ্রেপ্তার করতে হলে অবশ্যই ‘যথাযথ প্রমাণ’ থাকতে হবে। যেমন ‘প্রত্যক্ষদর্শী’, ‘ভিডিও’, ‘ছবি’ এবং এর সঙ্গে অবশ্যই ‘ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের’ অনুমতি থাকতে হবে। নিঃসন্দেহে এই উদ্যোগ ২০২৪ সালের আগস্ট–সেপ্টেম্বর মাসেই বাস্তবায়িত হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল।
পুলিশের ওই নির্দেশনাকে সংবিধানবিরোধী উল্লেখ করে হাইকোর্টে আবেদন করা হয়। হাইকোর্ট পুলিশের ওই নির্দেশনা স্থগিত করেন। তবে এর পর থেকে সরকার স্থগিতাদেশের বিরুদ্ধে আপিল করেনি। আইন পরিবর্তনের জন্য কোনো অধ্যাদেশও জারি করেনি।
সরকার গত ১০ জুলাই ফৌজদারি কার্যবিধি সংশোধন করে। এর মাধ্যমে একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাকে অনুমতি দেওয়া হয় যে ‘প্রাথমিক তদন্ত’ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ‘প্রমাণ অপর্যাপ্ত’ বলে প্রমাণ করলে তিনি (কর্মকর্তা) সেই ব্যক্তির নাম এফআইআর থেকে বাদ দিতে পারবেন। এটি স্বাগতযোগ্য পদক্ষেপ, তবে সংশোধিত আইনটি এখনো ত্রুটিপূর্ণ গ্রেপ্তার বন্ধ করতে পারেনি। প্রমাণ ছাড়া আটক ব্যক্তিদের সহায়তা করতেও কোনো উদ্যোগ নিতে পারেনি।
সমানভাবে উদ্বেগজনক বিষয় হলো জামিন দেওয়ার ক্ষেত্রে বিচারিক ব্যবস্থার দুর্বলতা, বিশেষ করে যখন অভিযুক্ত ব্যক্তি জাতীয়ভাবে পরিচিত। ম্যাজিস্ট্রেট ও জেলা আদালত কখনো জামিন দেন না; অন্তত জাতীয়ভাবে পরিচিত কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে দেওয়া হয় না। হাইকোর্টের বেঞ্চগুলো তুলনায় জামিন প্রদানে বেশি অনুকূল। তবে কিছু কারণে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মুক্তি দেওয়া সম্ভব হয় না। যেমন অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয় সব অন্তর্বর্তী জামিন আদেশ স্থগিতের আবেদন করে; আপিল বিভাগ অন্তর্বর্তী জামিন আটকানোর সেসব আবেদন মঞ্জুর করে এবং সেই সঙ্গে নতুন কোনো মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পুলিশের গ্রেপ্তার দেখিয়ে দেয়।
এ সবকিছুই ভিন্নভাবে করা যেত। সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর খুব শিগগির আইন পরিবর্তন করে কেন্দ্রীয়ভাবে একটি তদন্তব্যবস্থা চালু করা উচিত ছিল, যেখানে স্থানীয় পুলিশ কর্মকর্তাদের ওপর নির্ভর না করে বিশেষজ্ঞ তদন্তকারী দলের মাধ্যমে শুধু যথেষ্ট প্রমাণ থাকা ব্যক্তিদেরই গ্রেপ্তার করা হতো। এ কথা এখন বলা হচ্ছে, বিষয়টি এমন নয়। ৫ আগস্টের মাত্র কয়েক সপ্তাহ পরই সরকারের উপদেষ্টাদের কাছে এ প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল।
আরেকটি উদ্বেগজনক বিষয় হলো সরকারের পক্ষ থেকে জারি করা একটি আদেশে বিক্ষোভকারী ও অন্যদের আন্দোলনকালে এবং তার পরবর্তী সহিংসতা, হত্যাসহ সংঘটিত অপরাধ থেকে দায়মুক্তি দেয়। সত্যিই এমন দায়মুক্তি দেওয়া হয়ে থাকলে তা সব ধরনের ন্যায়বিচার প্রক্রিয়ার নীতির বিরোধী।
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল
সাধারণ আদালতের তুলনায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের কাজ সুষ্ঠু প্রক্রিয়ায় হচ্ছে। আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন, ১৯৭৩ ব্যাপকভাবে সংস্কার করা হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক আইনগত মানদণ্ডের সঙ্গে আরও সংগতিপূর্ণ করা হয়েছে।
এর নিজস্ব একটি তদন্ত সংস্থা রয়েছে এবং গত ২৫ জুন পর্যন্ত মোট ৭৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ট্রাইব্যুনাল মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য বিচার কার্যক্রমও শুরু করেছেন। তিনটি পৃথক মামলায় প্রসিকিউটর মোট ২৩ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন। এর মধ্যে পলাতক সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও আছেন। এই বিচার কার্যক্রম যথার্থ প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে, যদিও বিস্তারিত স্পষ্ট হবে বিচার শুরু হওয়ার পর।
এরপরও বেশ কিছু উদ্বেগের বিষয় রয়েছে। আইনটিতে আরও সংস্কার প্রয়োজন। এ আইনে গ্রেপ্তার প্রমাণের ভিত্তিতে হওয়ার বাধ্যবাধকতা নেই। ফলে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের কর্তৃক বেশ কিছু গ্রেপ্তার অযথার্থ বলে মনে হচ্ছে। চূড়ান্ত রায় ছাড়া ট্রাইব্যুনালের অন্য কোনো সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিলের সুযোগ আইনে নেই। অপরাধসংক্রান্ত কিছু শব্দ আন্তর্জাতিক স্বীকৃত সংজ্ঞার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, যেমন ‘সুপিরিয়র রেসপনসিবিলিটি’ বা নির্দেশদান–বিষয়ক দায়ের ক্ষেত্রে। অনুপস্থিতিতে হওয়া বিচারের (ইন অ্যাবসেন্টিয়া ট্রায়াল) ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য আইনি সুরক্ষা যথেষ্ট নয়। এ ছাড়া ‘সাধারণ জ্ঞানের বিষয়’ (ফ্যাক্ট অব কমন নলেজ) কী হিসেবে বিবেচিত হবে, তার কোনো স্পষ্ট সংজ্ঞা নেই এবং বিচারিক বিজ্ঞপ্তি (জুডিশিয়াল নোটিশ) কীভাবে ব্যবহৃত হবে তা নিয়েও উদ্বেগ রয়েছে। মৃত্যুদণ্ডের শাস্তির বিষয়টিও অবশ্যই সমালোচনার বিষয়।
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের পূর্ববর্তী বিচারের সময় জামায়াতে ইসলামীর সাবেক আইনজীবী তাজুল ইসলামকে প্রধান প্রসিকিউটর পদে নিয়োগের বিষয়টি অনেকের জন্য উদ্বেগের কারণ হলেও তা নিজে থেকে স্বার্থবিরোধ সৃষ্টি করে না। বিচার শুরু হলে তাজুল ইসলামের কাজের ন্যায়পরায়ণতার সক্ষমতা সবার সামনে স্পষ্ট হবে। তিনি বাংলাদেশের অল্প কিছু আইনজীবীর মধে৵ একজন, আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আইন বিষয়ে যাঁদের ভালো ধারণা আছে।
তবে এ পর্যন্ত যে তিনটি অভিযোগপত্র আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশন দল প্রস্তুত করেছে, সেগুলোতে এমন বিবরণ রয়েছে, যা পড়লে মনে হতে পারে, এখানে আওয়ামী লীগের রাজনীতিকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর একটা প্রয়াস আছে; কিন্তু এ ধরনের বিষয় আদালতের সামনে আলোচ্য বা বিচারাধীন হতে পারে না।
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশন দলকে অবশ্যই অভিযুক্ত নারী–পুরুষের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগগুলোর ওপরই সতর্কভাবে মনোযোগ দিতে হবে এবং ভবিষ্যৎ বিচারগুলোতে রাজনৈতিক বিবেচনা এড়ানোর বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। নইলে অতীতের মতো একেও সমালোচনার মুখোমুখি হতে হবে।
সূত্র : প্রথম আলো
ইএইচ










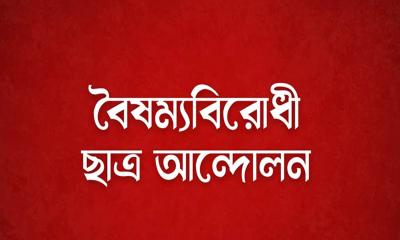

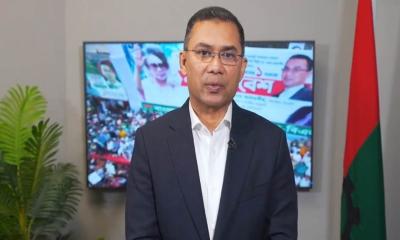






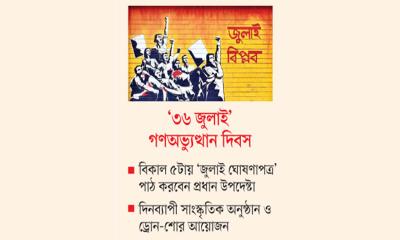










-20250730073418.jpg)